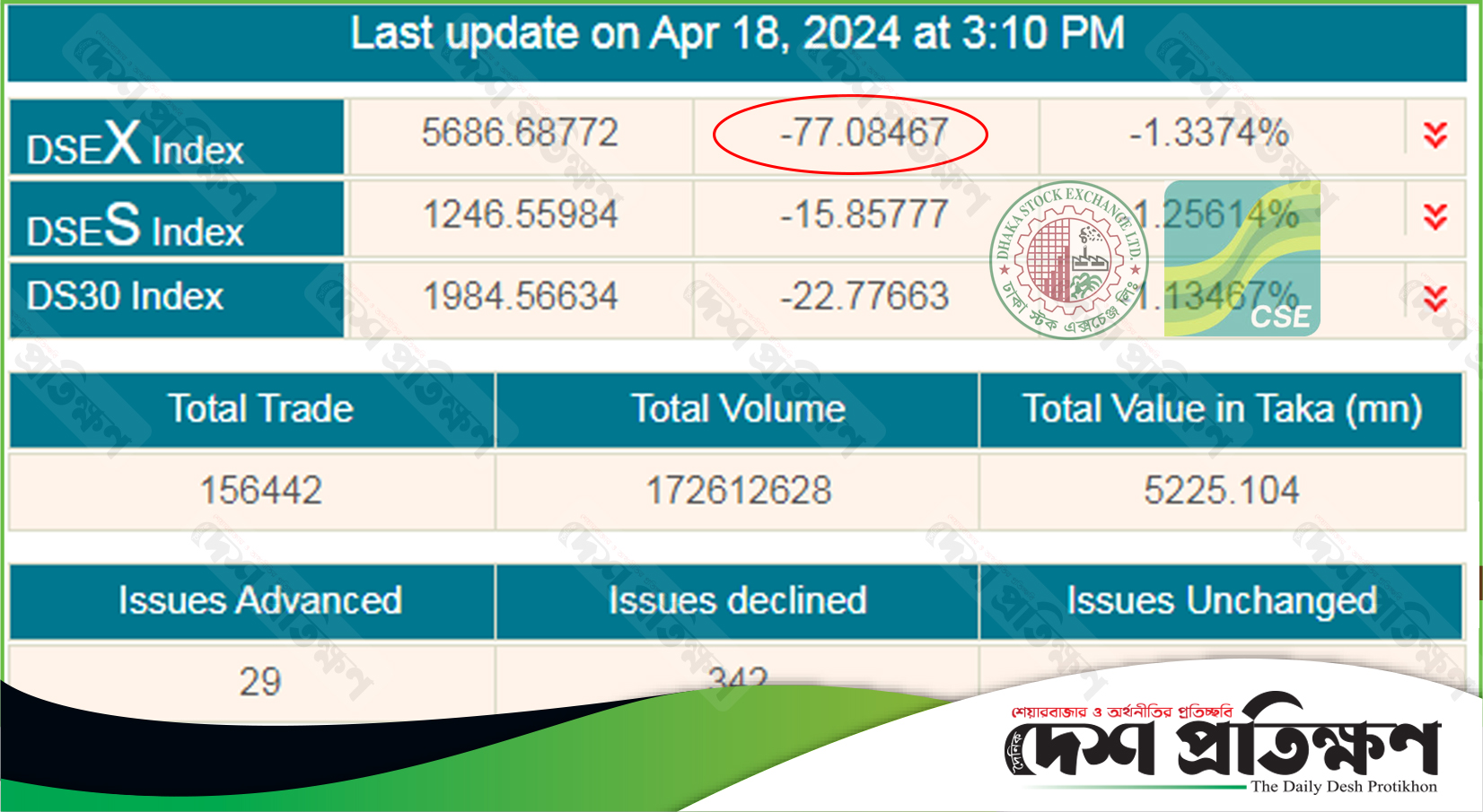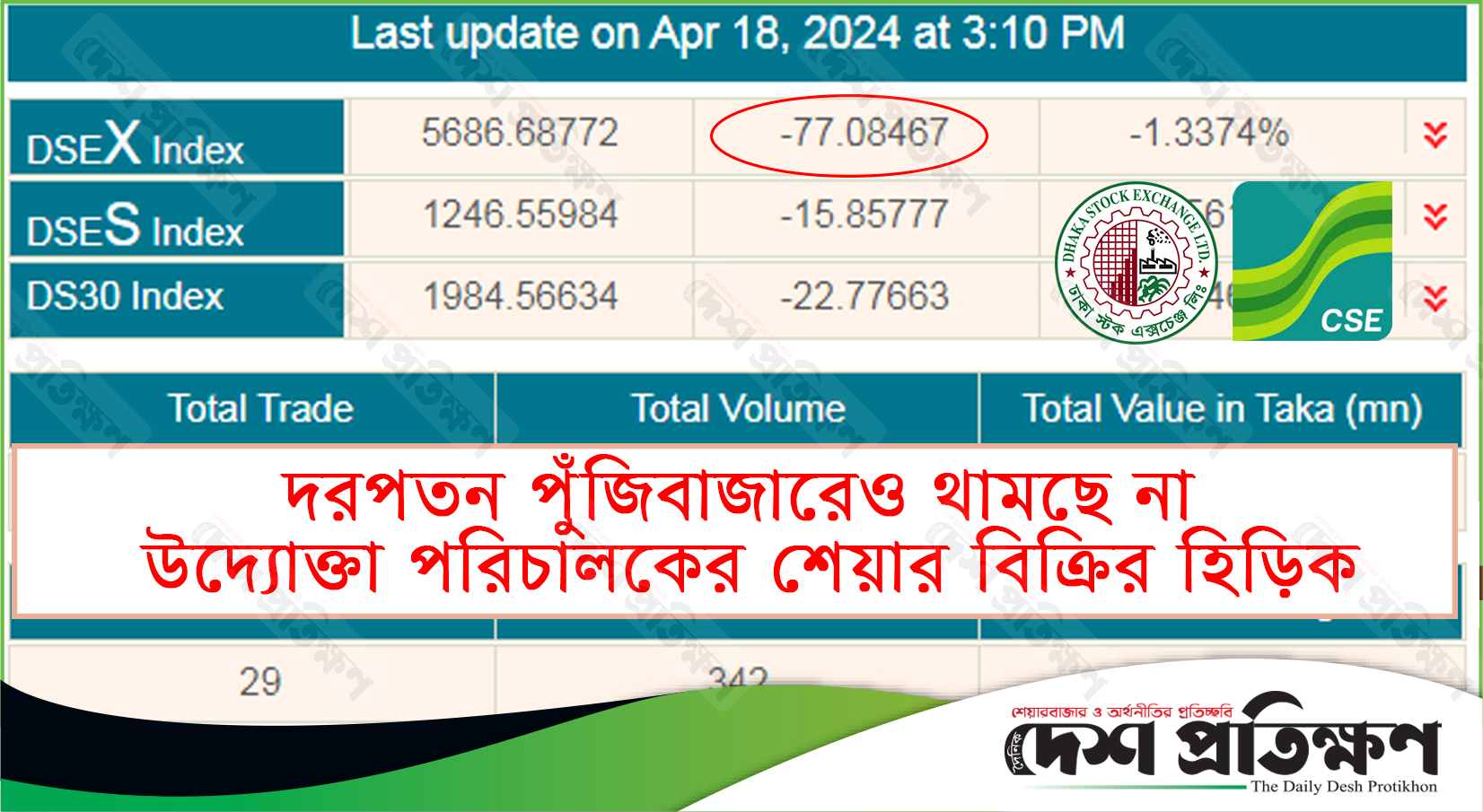এখন আমরা কী করব!
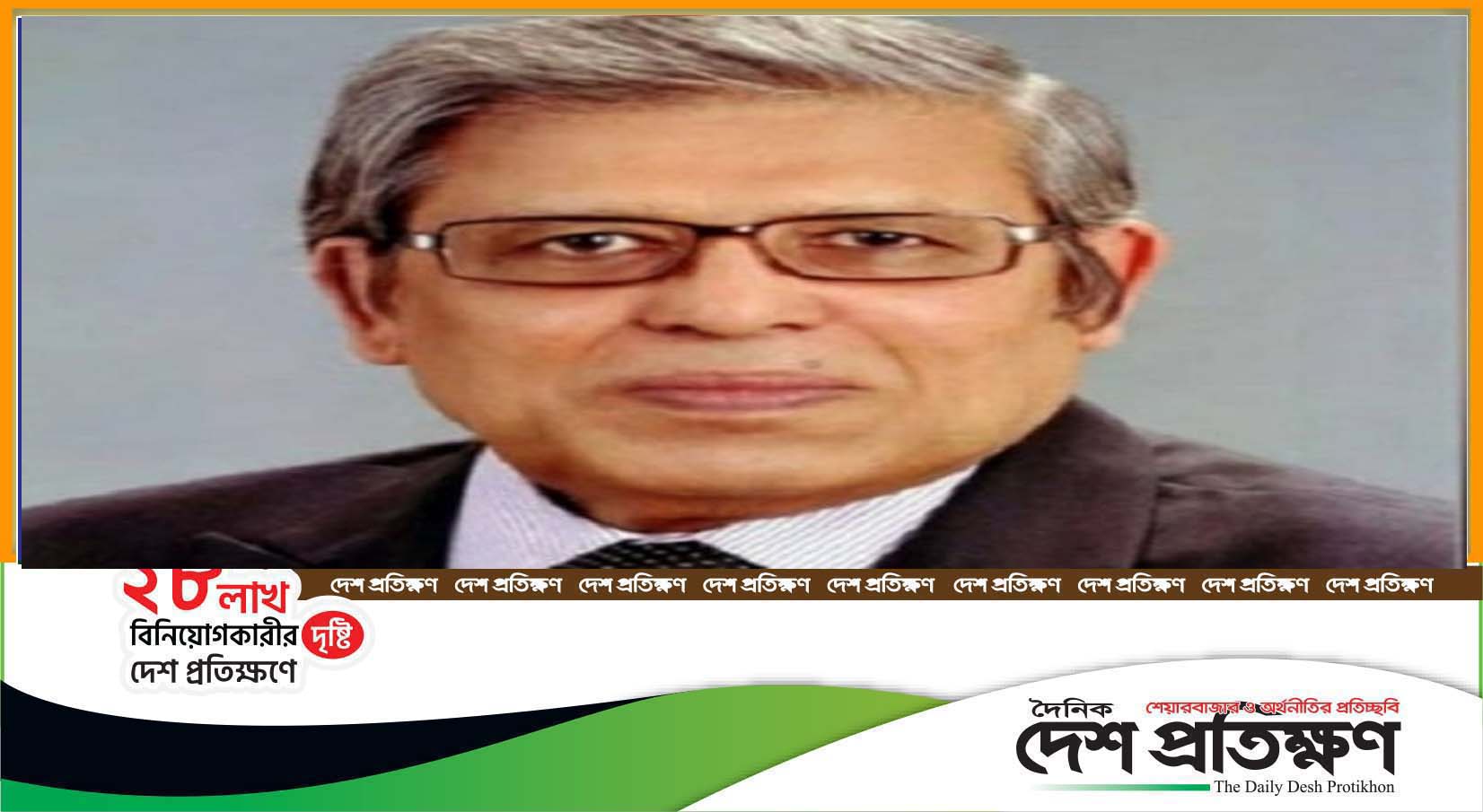
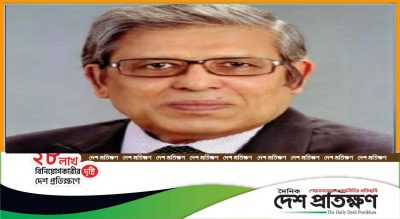 অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী: করোনার রাহু গ্রাস শুরুর আগে আমি ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে তিনটি ঘটনা নিজ চোখে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরার সম্প্রসারিত প্রকল্পের কোল ঘেঁষে একটি সনাতন গ্রাম সংলগ্ন মসজিদে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাস থেকে মাইল খানেক পূর্ব-উত্তরে এমন মজার বিষয় অবলোকন করব তা আমি ভাবিনি। সে দিন ছিল শুক্রবার। জুমার নামাজ পড়তে আমি সেই মসজিদে পা রাখলাম।
অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী: করোনার রাহু গ্রাস শুরুর আগে আমি ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে তিনটি ঘটনা নিজ চোখে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরার সম্প্রসারিত প্রকল্পের কোল ঘেঁষে একটি সনাতন গ্রাম সংলগ্ন মসজিদে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাস থেকে মাইল খানেক পূর্ব-উত্তরে এমন মজার বিষয় অবলোকন করব তা আমি ভাবিনি। সে দিন ছিল শুক্রবার। জুমার নামাজ পড়তে আমি সেই মসজিদে পা রাখলাম।
অজু সেরেই নিয়েছিলাম, তাই শুধু জুতা জোড়া হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতেই কিছু স্বেচ্ছাসেবক বললেন, ‘আমাদের মসজিদে জুতা রাখার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। আপনি জুতাগুলো বাইরে রেখে দিন’। আমি আপত্তি তুললাম। তারা আমাকে নিশ্চয়তা দিলেন, এই গাঁয়ে কোনো জুতা বা সেন্ডেল চোর নেই। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে জুতা বাইরে রেখেই মসজিদে ঢুকলাম।
ফিরে এসে আমার জুতা জোড়া অবিকৃত পেলাম আর অন্য সবাই মসজিদের বাইরে রাখা স্তূপ থেকে নিজ নিজ জুতা-সেন্ডেল খুঁজে নিলো। আমি একটু তাজ্জবই হলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল বহুদিন আগের আর একটি ঘটনার কথা। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি এবং মাঝে মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজে যেতাম।
সেদিনে তো বটেই, এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব মসজিদে জুতা রাখার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং এখনো আছে। চোর-ছ্যাচ্চোর থেকে জুতা বা সেন্ডেল রক্ষার জন্যে সেজদার সামনেই হয় বাক্স বানিয়ে বা অন্য কোনো ব্যবস্থায় জুতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কোনো কোনো মসজিদে তারপরও নির্দেশ আছে ‘জুতা সেন্ডেল নিজ দায়িত্বে রাখুন’।
বিষয়টি আমি তেমনটা পছন্দ করিনি কোনো দিন। আমার মনে হতো আল্লাহকে সেজদা না করে (আস্তাগফিরুল্লাহ) আমরা যেন আমাদের জুতা সেন্ডেলকেই সেজদা করছি। উপায় ছিল না, তাই আমি অনিচ্ছায় জুতা জুতার বাক্সে রাখতাম কিংবা আমার পাশে রাখতাম। সে দিন আমার এক জোড়া নতুন সেন্ডেল ছিল, তাই গুরুত্ব বিচারে আমি সেন্ডেল জোড়া অতি কাছে রেখেছিলাম। সেন্ডেল দুটির প্রতি অতি সতর্কতার কারণে আমার নামাজে আত্মনিবেদন বা নিমগ্নতা সম্ভব হচ্ছিল না।
তবুও দুরাকাত নামাজ শেষে আমি ক্ষাণিকটা অসতর্ক হয়ে পড়লাম। এই সুযোগে আমার পাশে বসা ব্যক্তিটি আমার সেন্ডেল জোড়া নিয়ে দিল ছুট। সবাই নামাজে, আমি আর কী করি। সেন্ডেল হারালাম আর মনে মনে বললাম অভাব বা স্বভাব মানুষকে খোদা ভীরুতা থেকেও বিরত রাখে না। আমার স্থির ধারণা হলো যে নতুন সেন্ডেলটি বিক্রি করে সে ধার্মিকবেশী চোর অধিক দাম পাবে বলেই আখেরাতের তোয়াক্কা না করে আল্লাহর ঘর থেকে চুরি করে ছুট দিল। অভাবের তাড়নায় যে তার ঝুঁকির কথা ভাবেনি।
অভাব তো এই দেশে দীর্ঘদিন ঝেঁকে বসেছিল। ছোটবেলার একটা গল্প বলি, আমি তখন সম্ভবত ক্লাস টুতে পড়ি। বছর খানেক আগে আমার বাবা মারা গেছেন; ক্যান্সারে মারা গেলেন, বিনা চিকিৎসায়। তখন ক্যান্সারের চিকিৎসা ছিল না। ছিল না কলেরা বা ওলাওঠার চিকিৎসা। কলেরাকে স্বনামে উচ্চারণ ছিল রীতিবিরুদ্ধ, বলা হতো ওলাবিবির আগমন। এই ওলাবিবির কারণে গ্রাম কী গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। ঝাড়ফুঁক থেকে শুরু করে হেন অপকাজটি নেই যা গ্রামের মোল্লা বা অন্য ধর্মের ধর্মগুরুরা করত না।
কত গাল গল্পের উৎস ছিল সেই ওলাবিবি। কেউ কেউ আজকের করোনার মতোই সেই ওলাবিবির সঙ্গে কথাও বলত এবং জেনে নিত কবে সে চলে যাবে। চোখ বুজে রায় দিত যে, অমুক দিনে ওলাবিবি চলে যাবে। এ দিয়ে অনেকে আর্থিক ও সামাজিক সম্মান সূচক ফায়দা লুটত। তখন গ্রামে আরও ছিল গুটি বসন্ত যার কোনো চিকিৎসা ছিল না। আমার বড় বোনের গুটি বসন্ত হয়েছিল।
তিনি সেরে উঠেছিলেন কিন্তু তার মুখে চিরদিনের জন্য গুটি বসন্ত চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। অল্পের জন্য তার চোখ দুটি রক্ষা পেয়েছিল। তখন কালাজ্বরের একমাত্র চিকিৎসা ছিল ধনীর জন্য ব্রহ্মচারী ইনজেকশন আর দরিদ্রদের জন্য মাথায় পানি ঢালা, আল্লাহ বা ভগবানের নাম জপা আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। তখন ম্যালেরিয়া ছিল, তবে ম্যালেরিয়ার জন্য কিছু চিকিৎসাও ছিল।
আমার বড় চাচা ডা. আদম আলী ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করতেন-সর্বোচ্চ আট আনা (বর্তমানে ৫০ পয়সা) ফি নিতেন, অধিকাংশ সময় গরিব মানুষ থেকে কোনো ফি নিতেন না। সময় সময় ফি তো দূরের কথা নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে রোগীদের ওষুধ বানিয়ে দিতেন। ওষুধ বানাতেন বিভিন্ন অনুপান (উপকরণ) মিশিয়ে হামান দিস্তায়। আমার মা তাতে সাহায্য করতেন। কার্যত মা ছিলেন বড় চাচার কম্পাউন্ডার। ডাক্তার চাচার এমন মনোভঙ্গির কারণে তিনি কোনো দিন সচ্ছল হতে পারেননি। দরিদ্রতা নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
তখন তো গাঁও-গেরামে প্রায় নব্বইভাগ লোকই ছিল দরিদ্র। ডাক্তারের ফি দেওয়া আর ওষুধ কেনার সামর্থ্য তাদের ছিল না। পেটে ভাতেও কাজ পাওয়া যেত না। খোদাভীরুতা প্রবল ছিল বলে চুরি, ডাকাতি কম ছিল, তবে যারা চুরি-ডাকাতি করত তারা প্রথমে জান বাঁচাতে, পরে নেশায় এবং সবশেষে স্বভাবে পেশাদার হয়ে যেত। তখন প্রবাদ ছিল ‘যক্ষ্মা হলে রক্ষা নেই’। যক্ষ্মাকে বোধ হয় এখনো ক্ষয় রোগও বলে। আমার বাবার ক্যান্সারের কথা বললাম আসলে তার ক্যান্সার হয়েছিল কিনা তা বুঝেছি বহু পরে।
ঝড়ে আমার বাবার পায়ে একটি মাদার গাছ পড়েছিল। কাঁটাযুক্ত এই গাছটি তার পায়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। সে ক্ষতটি আর শুকায়নি। তিনি একটি বড় এবং বলতে গেলে নিঃস্ব পরিবারের ভার আমার মায়ের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমার বাবা পড়াশোনার চেয়ে রাজনীতি বেশি পছন্দ করতেন। কংগ্রেস করতেন পাশাপাশি খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।
কুমিল্লায় অভয় আশ্রমে ঘাঁটি গেড়ে থাকা বড় বড় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তার চেনাজানা ছিল। রাজনীতি করলে জনকল্যাণ ছাড়া আত্মকল্যাণ করতে হয়, তা তার জানা ছিল না। তাই যখন তিনি বিয়ে করেন তখন তার কাছে বিত্ত বলতে পিতৃ প্রদত্ত সামান্য কিছু জমিজমা, গাই-গরু ও নগদ ফসলি উঁচু জমি ছিল। ধানের জমিগুলো ছিল নিম্নাঞ্চলে। গরু বাছুরের কোনো চিকিৎসা ছিল না।
তাই প্রতি বছরে আমাদের গাভী বা বাছুরের সংখ্যা ছিল কমতির দিকে। বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মা সবকিছুর দায়িত্ব নিতে চাইলে আমার বিত্তবান ও প্রভাবশালী নানা মাকে তার কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। ইসলামের বিধানমতো তার সম্পত্তির একটা অংশ মায়ের পাওনা ছিল। নানা প্রলোভন দেখালেন। মা নানার মতলব বুঝতে পারলেন। আটাশ কী ঊনত্রিশ বছর বয়সে মা বিধবা হয়েছেন বলে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালনের সুযোগ দিতে নানা এসেছিলেন।
আমার মা বেঁকে বললেন, কোনো অবস্থায় আমাদের মানে আমার পাঁচজন বোন ও আমাকে নিয়ে তিনি স্বামীর ভিটায় স্থিতি হলেন। আমি তখন নানার প্রাইমারি স্কুলেই ভর্তি হলাম। কিন্তু মায়ের ভালো লাগত না বলে তিনি আমাকে কাছে নিয়ে এলেন। বাড়ির কাছে দক্ষিণ চর্থার থিরাপুকুর পাড় প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। একবার প্রথমে খরায় ও পরে প্রবল বন্যায় আমাদের উঁচু জমি ও নিচু জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেল।
দেশেও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হলো। অতীতেও দেখেছি এমন অবস্থায় কারও সর্বনাশ ও কারও পৌষ মাস অবস্থা। টাউট বাটপারদের পৌষ মাস আর গরিবদের সর্বনাশ। ইউনিয়ন কাউন্সিলের তদানীন্তন প্রধানকে তখন বলা হতো প্রেসিডেন্ট আর ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বলা হতো মেম্বর। সৌভাগ্য আমার, আমাদের তখনকার চৌয়ারা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমার ফুফাতো ভাই সম্পর্কিত আর বামিশা এলাকার মেম্বর ছিলেন আমার মামা। নানার বখে যাওয়া ছেলে আবদুল আজিজকে লোকে আড়ালে আবডালে যাকে আইজ্জা ডাকাত বলত।
তিনি আমার মায়ের সৎ ভাই ছিলেন। আমার নানার তৃতীয় পক্ষের একমাত্র সন্তান ছিলেন আমার মা, প্রথম পক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তানে প্রয়াত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে আমার পাঁচ মামা ও এক খালা ছিলেন। আমার নানার দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর ছিলেন ওয়াহাবি আর আমার নানা ছিলেন সুন্নি। আমার বুঝ হওয়ার পরও দেখেছি উভয় পক্ষ মারামারি করতে লাঠিয়াল পালন করতেন।
নানার লাঠিয়ালদের হুন্দবী বলা হতো। আমাদের কাছে তাদের ভালো মানের মানুষ বলে মনে হতো না। এ লোকগুলো ছিল সন্দ্বীপের আদি বাসিন্দা। নদীভাঙনে নিরুপায় লোকগুলো দলবদ্ধ হয়ে এসে নানার আশ্রয়ে চাষাবাদ ও লাঠিয়ালের দায়িত্ব নিয়েছিল। আমার জানামতে তাদের কেউ কেউ আইজ্জা ডাকাতের সঙ্গীও ছিল। ধান ভানতে শিবের গীত ছেড়ে এবার আসল কথায় আসছি।
সেবারের খরা ও বন্যায় ফসল ক্ষতির পর আমরা প্রথমবারের মতো চরম দরিদ্রের কোঠায় চলে গেলাম। মাঝে মাঝে আমাদের অনাহারে থাকতে হতো। আজকের মধ্যবিত্তদের মতো অভাবেও মুখ খুলে কারও কাছে কিছু চাইতে অন্তত আমার মায়ের প্রবল অনীহা ছিল। আমি জানি না তিনি কেন এমন আত্মমর্যাদা লালন করতেন আর সেটা যে আমার মাঝে সংক্রমিত হয়েছিল সে কথা অন্য কোনো দিন বলব। তিনি বলতে গেলে প্রায়শ লুকিয়ে লুকিয়ে আধপেটা থাকতেন। বয়সে ছোট হলেও বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে এড়িয়ে যেত না।
একদিন চুপিচুপি আমি রিলিফের চাল বা গম পেতে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। সবার সঙ্গে আমি প্রতিবেশী ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের বিশাল গুদাম ঘরের সামনে লাইনে দাঁড়ালাম। সাহায্য প্রার্থীদের লাইন থেকে আমাকে অন্যেরা ঠেলেঠুলে আরও পেছনে ফেলে দিচ্ছিল। কিছু না বলে বরং মুখ লুকোতেই আমি ব্যস্ত ছিলাম।
কারণ, তা না হলে চাউর হয়ে যাবে যে, অমকের ছেলে বা অমকের নাতি রিলিফের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে। খবর জানাজানি হলে মা আমাকে বেদম না হলেও, প্রচুর পিটুনি দেবেন। বেলা গড়িয়ে পড়ার পর আমার রিলিফ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো। টাউট বাটপারদের পাশর্^ প্রতিদানের বদলে আগেই কিছু রিলিফ সামগ্রী অন্যরা পেল।
আমার হাতে কোনো পয়সা ছিল না। তাই আমার অন্যকে কী দিয়ে ম্যানেজ বা সামলানোর উপায় ছিল না। সারা দিন না খেয়ে থাকায় আমার মেজাজটা চরম তিরিক্ষে ছিল। দুর্ভাগ্য আমার, আমার মুখের সামনেই গুদামের দরজা বন্ধ করে আমাকে পরের দিন ধরনা দিতে বলা হলো। এবারে প্রবল বাধা এড়িয়ে আমি ইউনিয়ন কাউন্সিলরের প্রেসিডেন্ট ও মেম্বরের সামনে হাজির হয়ে রিলিফ দাবি করলাম। প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে চিনেও না চেনার ভান করলেন; অবশ্য মামা আমাকে এড়াতে পারলেন না।
সৎ ভাই হলেও তিনি আমার মাকে বড্ড আদর করতেন এবং আমাদের ব্যাপারে তিনি অতি স্নেহের ব্যবহারই করতেন। একবার আমার হাত থেকে মাগুর মাছ ফসকে গিয়ে তার হাতে গেঁথে বসল। সেদিন আইজ্জা ডাকাতের স্বরূপ দেখার সুযোগ হয়েছিল। তার রক্তাভ চোখ আর তর্জনগর্জন দেখে আমি এতটা ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি আমার প্রস্রাব ধরে রাখতে পারিনি। ক্ষাণিক পরে তিনিই বললেন, ‘অমুকের ছেলে বলে আজ তুই বেঁচে গেলি’। সেই আজিজ মেম্বারের সম্মুখীন হলাম। তিনি আমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।
অতি সন্তর্পণে বাড়ি ঢুকলাম। মা রেগে থাকলেও আমার শুকনো মুখ দেখে কিছু বললেন না। নিজে না খেয়ে আমার জন্য তুলে রাখা খাবারগুলো আমাকে খাওয়ালেন। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছিল, চোখের পানি সামলাতেও কষ্ট হচ্ছিল। তবুও আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম এ কারণে যে, ভিক্ষুকের লাইনে দাঁড়িয়ে রিলিফ প্রার্থনার কথা তাৎক্ষণিক তিনি জানতে পারেননি। বেদম পিটুনি থেকে বেঁচে গেলাম। তবে এ কথা বহুদিন পরে আমার মা জানতে পেরেছিলেন। আমার এক আত্মীয়ের পরামর্শে আমি মামাদের কাছে জাকাত চাইলাম।
মার সামনেই আজিজ মামা আমাকে জাকাত পাওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা দিলে এবং রিলিফ সামগ্রীর জন্য আমার লাইনে দাঁড়ানোর গল্পটা ফাঁস হয়ে গেল। মা তার ভাই ও আত্মীয়দের সামনে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন না ঠিকই, কিন্তু বারণ করে দিলেন আমি যেন কোনো দিন আর ভিক্ষুকের মতো কারও কাছে হাত না পাতি। কী মোক্ষম শিক্ষা, আর কী সার্থক শিক্ষিকা। আর আমি জীবনে কারও কাছে কদাচিত হাত পাতিনি। নবীন শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় সামনে আমার ডান হাতটি চিত করে বলি ‘এটা ফকিরের হাত’ আর উপড় করে দেখাই ‘এটা ভিক্ষুকের হাত’।
তাদের উপড় করা হাতের অধিকারী হতে শিখাই। মায়ের শিক্ষার নিবেদিত অনুশীলন। পরে সংসার চলল কীভাবে তা বলতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে; তা ছাড়া আমি এমন কেউকেটা পরের জীবনে হইনি যে, আমার কথায় কেউ শিউরে উঠবে বা আহা উঁহু করবে। তবে বিকল্প খুঁজে নিয়েছিলাম, চুরি বা ডাকাতি নয়, সমাজ স্বীকৃত কঠোর জীবন ও জীবিকা দিয়ে। তারপর থেকে আমি দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভাঙার চেষ্টা করেছি।
দরিদ্রকে নয় দরিদ্রতাকে প্রচ- ঘৃণা করেছি এবং তাকেই বিমোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও যুদ্ধকালে বহু প্রাপ্তির কথা মনে দোলা দিত, দারিদ্র্য বিমোচন ছিল অন্যতম। আরও ছিল রোগমুক্ত, কুসংস্কার মুক্ত সমাজ। তাই তো বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাবস্থায়ও সুখের দিনে মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম। প্রত্যাশা ছিল- একদিন দারিদ্র্য আমাদের ছেড়ে যাবে।
দেশ শত্রুমুক্ত হলো, বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে ফিরে এলেন। অনেক কাজের মাঝে দারিদ্র্য মুক্তির ইরাদা নিয়ে যখনই আগাচ্ছিলেন, তখনই কুচক্রীমহল তাকে সপরিবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। আমার প্রত্যাশা ছিল বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে ১৯৮২ কী ১৯৮৩ সালে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা শতকরা বিশ ভাগে নেমে আসবে। আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে সশাসিত হয়ে দুবেলা দুমুঠো ভাত খাওয়া, মাথা গোঁজার ঠাঁই, রোগে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সবার সঙ্গে বসবাস করা। চেষ্টা করেছি অনেক।
একবার দেশে তিষ্টিতে না পেরে বিদেশ চলে গেলাম। কিছুটা তিষ্টের অধিকারী হলাম। নিজের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করলাম। আন্দোলন সংগ্রামে জড়িয়ে ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার আর তার উত্তরসূরিদের ক্ষমতায় এনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও তাদের দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন-সর্বাগ্রে দারিদ্র্য বিমোচন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা তিমির আঁধারের বুক চিরে ক্ষমতায় এলেন।
বঙ্গবন্ধুর মতো তিনি অনেক কিছুর সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনে হাত দিলেন ও ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাসীন থেকে আশিভাগ দরিদ্রতাকে প্রায় বিশ ভাগে নামিয়ে আনলেন; যার কারণে চুরি-চামারি কমে এলো; যার কারণে ঢাকার অভ্যন্তরেও মসজিদ থেকে জুতা সেন্ডেল চুরি প্রশমিত হলো, গ্রামে ফকির উড়ে গেল। স্বভাবের কারণে বা ব্যবসায়ের ফিকিরে তারপরও ঢাকা শহরে কিছু ফকির দেখা যেত। এসব ফকিরকে পয়সা কম দিলে ছুড়ে ফেলে দিত কিংবা কটুকথা শোনাত। তাই আমি অন্তত এক টাকা, দু-টাকা ভিক্ষা দিতাম না। আমি ভিক্ষুকদের স্বাবলম্বী হওয়ার পরামর্শ দিতাম; পারলে একটু বড় অঙ্কের অনুদান দিতাম।
করোনার দৌরাত্ম্য শুরুর আগে কুমিল্লা গেলাম তিনবার। প্রতিবারেই হাতে কিছু ভাংতি টাকা নিলাম যাতে সেখানে ফকির মিসকিনকে দিতে পারি। প্রথমবার একটি রেস্তোরাঁয় সপরিবারে খাবার খেয়ে আমি ফকির খুঁজতে শুরু করলাম। ধারে কাছে কাউকে না পেয়ে একটি ছেলে নজরে পড়ল যে লাঠি ভর করে হাঁটছে। আমি তাকে সাহায্যপ্রার্থী ভেবে কিছু টাকা দিতে গিয়ে বেকুব বনে গেলাম। ছেলেটি বলল ‘আমি ভিক্ষুক নই, পায়ে ব্যথার কারণে লাঠি ভর করে হাঁটছি’।
তারপরের সপ্তাহে আবারও কুমিল্লা যেতে হলো। রামিশায় বসবাসরত আমার খালাতো ভাইয়ের জানাজায় শরিক হতে কুমিল্লার পথে যাত্রা শুরু করলাম। জানাজার পর কিছু গরিব ফকির মিসকিন আসবে জেনে কয়েক হাজার টাকা খুচরা হাতে করে নিলাম। প্রতিটির মান ছিল পঞ্চাশ কী একশ টাকা। আমার মনে বোধ ছিল কম টাকা ফকির মিসকিনরাও নেবে না।
যাক রামিশায় পৌঁছলাম এবং জানাজার নামাজের জন্য জুতা জোড়া খুলে মসজিদে প্রবেশে উদ্যত হলাম। অভ্যাসবশত জুতা জোড়া খুলে হাতে নিয়ে সুনির্দিষ্ট বাক্সে ফেলে রাখব ভেবে জুতায় হাত রাখলাম। বেশ কজন ছুটে এসে বলল, ‘আমাদের এখানে জুতার বাক্স নেই, জুতা আমরা মসজিদের বাইরে রাখি এবং জুতা চুরি হয় না।’ আমি অবিশ^াস নিয়েও ঢাকার উত্তরার পূর্ব বর্ণিত ঘটনাটির কথা স্মরণ করে জুতাজোড়া রেখে নামাজ পড়লাম এবং ফিরে এসে আমার জুতা জোড়া পেয়ে গেলাম। বিস্মিত হলাম বৈকি। আশপাশে ভিক্ষুক খুঁজেও কাউকে পেলাম না। ভাবলাম হয়তো তারা খবর পায়নি।
সেহেলামে গিয়েও জুতা চোর পেলাম না। ভিক্ষুকও পেলাম না। এবারে কাউকে ফিস ফিসিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল, দেশে এখন আর ছোটখাটো বা ছিঁটকে চোর বা ফকির নেই। দেশ বলতে সব বাঙালির মতো তারা নিজের গ্রাম ও পারিপাশির্^কতাকে বুঝিয়ে ছিল। আমি ভাবলাম আল্লাহ মেহেরবান। তারই করুণায় শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছে এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে অন্ততপক্ষে দারিদ্র্য ও ছোটখাটো চুরি-চামারি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।
এ ঘটনাগুলোর মাস খানেকের মাথায় করোনা নামে মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন আমরা হয়েছি। মানুষের আয়-রোজগার থেমে গেছে। দীনহীনরা তো বটেই, ছোটবেলায় আমাদের মতো টনটনে মান-মর্যাদা মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্তরাও সরকারি সাহায্য পাচ্ছে ও নিচ্ছে। টাকা বা সামগ্রীর বিচারে এই সাহায্য একেবারে কম নয়। তবুও দানের সামর্থ্য কিন্তু কমছে। আয়-উপার্জন সংকুচিত হচ্ছে, সরকারি কোষাগারেও একদিন টান পড়বে। আমার মা বলতেন আয়-উপার্জন ছাড়া খুঁটে খুঁটে খেলেও রাজ-ভান্ডারে একদিন টান পড়বেই।
পরের ঘটনা, গত কদিনের চুরি-চামারির সংখ্যা বাড়ছে বলে শুনেছি, ভিক্ষুকের সংখ্যাও বাড়ছে। নিজ চোখে দেখলাম ভিক্ষুকের ভিড় আর ভিক্ষাসামগ্রী লুফে বা লুটে নিতে করোনাকে তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য। বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনলাম ঢাকা শহরে তো বটেই গ্রামেও ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রম বর্ধমান। এই সংখ্যাটা যদি বাড়তে বাড়তে আমার শৈশবের অবস্থায় পৌঁছে যায়, তাহলে মরেও শান্তি পাব না। ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য সামাজিক দুর্বৃত্তপনা বাড়বে নিঃসন্দেহে। আমার ধারণা আমার পূর্বসূরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ বাংলার সুহৃদগণ স্বর্গে বসেও অস্বস্তিতে ভুগবেন। তাহলে এখন আমরা করব কী!
লেখক : মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য।